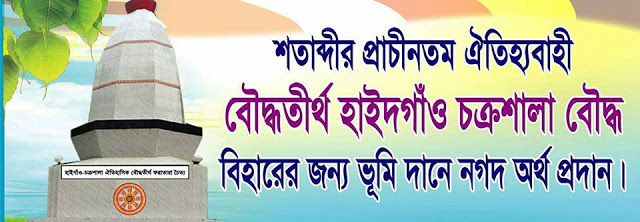by admin | Jan 9, 2019 | blog
গুরুভন্তের দেশনাঃ অকালমৃত্যু কাদের হয় না/কারা দীর্ঘায়ু হয়???
বুদ্ধ ধাতু জাদী, পুল পাড়া, বান্দরবান। ০৪/০১/২০১৯ইং
মহাধর্মপালা জাতক থেকে
সংসার সমুদ্রে সবই অনিত্য। অনেকে ছোটকালেই অবুঝ বয়সে মারা যান, কেউবা মধ্য বয়সে। শুধু তাই নয় পৃথিবীর আলো না দেখে মায়ের পেটেই মৃত্যু ঘটে অনেকের। অল্পায়ু হলে নিজে যেমন পুণ্যকর্ম করতে পারে না, পরিবারেও কাজে আসে না, পরিবারের সদস্যদের সীমাহীন দুঃখ-কষ্টও সহ্য করতে হয়।
ধর্মচারী ব্যক্তি ধর্মপাল। ধর্মপাল বোধিসত্ব হয়ে জন্ম নেন। তাঁর নামেই গ্রাম। তাঁর পিতার নাম মহাধর্মপাল। ধর্মপালের পুরো বংশ অর্থাৎ পরিবার-আত্মীয় পরিজন সকলেই ১০ প্রকার কুশল কর্মে সর্বদা নিয়োজিত এবং ১০ প্রকার অকুশল কর্ম থেকে বিরত ছিলেন।
একসময় ধর্মপাল ১৬ বছর বয়সে তক্ষশীলায় বিদ্যাশিক্ষা নিতে যান। অল্প সময়ে তিনি যত রকমের বেদ-বিদ্যা ছিল সবই আয়ত্ত করেন। একদিন ধর্মপালের গুরু অর্থাৎ আচার্যের বড় ছেলে কম বয়সে মারা যান। তিনি ধর্মপালেরই সহপাঠী ছিলেন। মরদেহ শ্মশানে নেয়ার সময় সবাই কান্না করছিল। কিন্তু ধর্মপাল কান্না না করে ধীর-গম্ভীরভাবে স্বাভাবিক হয়ে ছিলেন। তাঁর এই স্বাভাবিক নির্লিপ্ত আচরণে সবাই অবাক হল। তাঁর এই নির্বিকারের কারন জানতে চাইলে তখন তিনি বলেন, আমাদের বন্ধু-সহপাঠী অকালে মারা গেছেন। এতে দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। তারা বললেন, সংসারে সবই অনিত্য তা ঠিক আছে, তাই বলে এত অল্প বয়সে একজন জ্ঞানী-গুণী মারা গেছে তোমার দুঃখ লাগছে না!!!
তখন ধর্মপাল বলেন, এত অল্প বয়সে আমাদের পরিবারে, বংশে কেউ মরে নি। সবাই বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছে। একথা শুনে ধর্মপালের গুরু ঠিক করলেন তিনি ধর্মপালের গ্রামে যাবেন। গিয়ে দেখবেন এর কারণ কী। তবে যাওয়ার সময় আচার্য মৃত ছাগলের হাড়গোড় নিয়ে চললেন।
বাড়িতে গেলে ধর্মপালের পিতা মহাধর্মপাল ও তাঁর লোকজন অত্যন্ত শ্রদ্ধারর সাথে ভেতরে নিয়ে আগন্তুকের সেবা যত্ন করলেন। আচার্য নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আপনার ছেলে ধর্মপাল মারা গেছে। সেকথা শোনার সাথে সাথে মহাধর্মপাল হা হা হা করে অট্টহাসি হাসলেন। আচার্য অবাক হলেন। তিনি সাথে নিয়ে আসা হাড়গোড় দেখিয়ে বললেন এই হাড়গোড় ধর্মপালের দেখুন। তবুও মহাধর্মপাল কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। বরং বললেন আমাদের বংশে ১০০ বয়স না হয়ে কেউ মরেনি। তাই আমি বিশ্বাস করিনা যে আমার ছেলে মারা গেছে। আচার্য বললেন, হ্যা মহাধর্মপাল আমি মিথ্যা বলেছি আপনাকে। আপনার ছেলে মরেনি। তাহলে আপনি আমাকে বলুন কীভাবে আপনারা দীর্ঘায়ু জীবন লাভ করে থাকেন।
তখন মহাধর্মপাল বললেন, আমরা, আমাদের বংশের সবাই সবসময় দানকর্ম, শীল পালন করে থাকি। সদাসর্বদা মিথ্যা বলা থেকে, সকল প্রকার অকুশলকর্ম থেকে, খারাপ আচরণ করা থেকে বিরত থাকি।
আমরা বাল-মূর্খদের সংস্পর্শে যাই না, তাদের সাথে কথাও বলি না। তারা যদি কিছু বলেও আমরা শুনি না, প্রতিপালন করি না। আমরা সাধু-সজ্জন, ধার্মিক, গুণী, শীলবান, পুণ্যবান, সৎপন্ডিতের সংস্পর্শে থাকি, সান্নিধ্যে থাকি, তাদের কথামত চলি, সে হোক গরীব অথবা ধনী।
আমরা দান দেয়ার আগে পূর্বচেতনায় আনন্দিত হয়ে সুন্দর চেতনা রাখি। দান দেয়ার সময় এবং দেয়ার পরও উৎফুল্ল, আনন্দিত হই। অর্থাৎ দানের পূর্ব চেতনা, মুঞ্চচেতনা এবং অপর চেতনায় সদাসর্বদা উৎফুল্ল থাকি। যদি বাড়িতে সাধু-সন্ন্যাসী-অচেনা পথিক আসে তাদের অন্নব্যঞ্জন, আহার না দিয়ে, সেবা না করে যেতে দিই না।
তিনি আরও বললেন, আচার্য আমি নিজেও আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য নারী, আমার স্ত্রীও আমাকে ছাড়া অন্যপরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনা। তাই আমাদের অকালমৃত্যু হয় না।
হে আচার্য, আমরা প্রাণী হত্যাও করি না। আমরা অন্যের সম্পদ চুরি করি না। এমনকি স্থানচ্যুতও করি না।
আমরা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলি না। অন্যের সম্পদ হরণ করি না। আমরা এই চার রকমের রীতি পালন করি বলে আমাদের অকালমৃত্যু হয় না। ভগবান বুদ্ধ তখন জীবিত ছিলেন না। জগৎ রক্ষা করত এই পঞ্চশীলই। তীর্যকলোক, প্রেতলোক, অসুরলোক, নরকলোক এই চার অপায়ে যেতে হবে বলে আমরা সদাসর্বদা সত্য পথে, ধর্ম পথে চলি। শুধু আমরা নই আমাদের সেবাকারী দাস-দাসীরাও পঞ্চশীল ভঙ্গ করে না।
পঞ্চশীল পালন করেই আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে রক্ষা করি। কথায় আছে, যিনি ধর্ম পালন করেন ধর্ম তাকেই রক্ষা করেন। এরূপ দান, শীলসহ ১০টি কুশলকর্ম করে থাকি। এবং ১০টি অকুশল কর্ম করা থেকে বিরত থাকি। রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতেও আমরা ধর্ম পালন করে থাকি। কুশল কর্মের মাধ্যমে আমরা পুণ্য সঞ্চয় করি তাই আমরা দীর্ঘায়ু লাভ করি।
এই ১০ রকমের কুশলকর্মগুলো হলঃ
১/প্রাণী হত্যা না করা
২/চুরি না করা
৩/ মিথ্যা কথা না বলা
৪/মিথ্যা-কামাচার থেকে বিরত থাকা
৫/পিসুনবাক্য না বলা। অর্থাৎ দুজনের মধ্য বিভেদ সৃষ্টি না করা।
৬/ফারুসাওয়াচা না করা। গালিগালাজ, অশ্রাব্য ভাষা, কটুক্তি, অশ্লীল কথা বলা থেকে ববিরত থাকা। যেমনঃ বংশের/মা-বাবার নাম তুলে গালিগালাজ না করা।
৭/ তুচ্ছ, মূল্যহীন কথা না বলা। অর্থাৎ নির্বাণপ্রদায়ী ধর্মকথা বলা।
৮/হিংসা না করা, অন্যের সম্পত্তি আত্মসাৎ না করা।
৯/অন্যের ক্ষতি না করা, প্রাণনাশের হুমকি না দেয়া।
১০/ মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন না হয়ে নির্বাণ পথগামী সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া।
আর এই ১০ রকমের কুশলকর্মের বিপরীত হচ্ছে ১০টি অকুশল কর্ম।
হে আচার্য বুদ্ধের নির্বাণপ্রদায়ী ধর্মের ত্রি-শাসন (পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি, প্রতিবেধ)কে যিনি রক্ষা- চর্চা করবেন তাঁর অকালমৃত্যু হবে না। তখন আচার্য বললেন, মহাধর্মপাল আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে এই শিক্ষা দিন। এরপর আচার্য ১০ রকমের কুশল ও অকুশল কর্মের শিক্ষা নিয়ে ফিরে গেলেন তক্ষশীলায়।
সাধু সাধু সাধু
Copypost : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুক থেকে সংগৃহীত ।

by admin | Jan 8, 2019 | blog
একসময় সর্বজন পূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সমবেত দায়ক দায়িকাবৃন্দের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনা প্রদানকালে বলেন-তোমাদেরকে ধর্মদেশনা প্রদান করার ইচ্ছা হচ্ছে না আমার। কারণ দেশনা প্রদান করলেও তোমরা সেটা বুঝতে পারবে না। তারপরও আমি মন চিত্ত সম্বন্ধে বলছি,ভালোরূপে শ্রবণ কর। মন চিত্ত কি? সাধারণত মন চিত্ত চঞ্চল,এক স্থানে থাকে না। সর্বদা বিষয় হতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে। চিত্ত কেন সেভাবে ঘুরে বেড়ায়? চিত্ত দুঃখ পায় বলে সেভাবে ঘুরে বেড়ায়। প্রায় লোকজনকে বলতে শুনা যায়-‘আমি কি করব, আমি কোথায় যাবো, আমি কোথায় অবস্থান করবো? প্রকৃতপক্ষে লোকজনেরা এসব কথা বলে না, তাদের মন চিত্তই এসব চিন্তা করে। চিত্ত যদি তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হতে না পারে, তাহলে মাররাজ্যে অবস্থান করবে, এভাবে সর্বদা ঘুরে বেড়াবে।
তোমরা কোথা (কোন লোক) হতে এসে বর্তমানে এই জন্মগ্রহণ করেছ? সাধারণতঃ কেউ কামলোক হতে, কেউ রূপলোক হতে, কেউ বা অরূপলোক হতে চ্যুত হয়ে বর্তমান এই জন্মগ্রহণ করেছ। তোমরা যেইজন যে লোক হতে চ্যুত হয়ে এসেছ তার চিত্তে সেইরূপ স্বভাব বিদ্যমান থাকবে। কামলোক হতে আসলে কামলোকের স্বভাব, রূপলোক হতে আসলে রূপলোকের স্বভাব,আর অরূপলোক হতে আসলে অরূপলোকের স্বভাব; এমন কি তির্যক প্রাণী, যেমন-বানর হতে আসলে বানরের স্বভাব, হাতি হতে আসলে হাতির স্বভাব, বাঘ হতে আসলে বাঘের স্বভাব, বিড়াল হতে আসলে বিড়ালের স্বভাব, ময়না হতে আসলে ময়নার স্বভাব থাকবে। পূর্বজন্মের স্বভাব থেকেই যাবে, সেই স্বভাবকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা যাবে না। বুঝতে পারছ তো? আমি দেখছি, তোমাদের প্রত্যেকের চিত্ত তৃষ্ণায় জট বেঁধে রয়েছে। সেই তৃষ্ণায় জট বাধা অবস্থা হতে চিত্তকে মুক্ত করতে পারবে কি তোমরা? পারবে না। চিত্ত যদি তৃষ্ণার জট দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাহলে চিত্ত দুঃখ পায় বা দুঃখগ্রস্ত হয়। সেই দুঃখাবস্থা হতে মুক্ত হবার জন্যে চিত্ত ছট্ফট্ করে। অন্যদিকে চিত্ত যদি অবিদ্যার জটে আবদ্ধ থাকে, তাহলে চিত্ত পাপকর্মের দিকে প্রভাবিত হয়, সর্বদা পাপকর্ম সম্পাদন করতে থাকে, দুঃখমুক্তি নির্বাণ লাভ বুঝতে পারে না, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, জায়গা-জমি নিয়ে যারপরনাই ব্যাপৃত থাকে।
কয়েক মাস পূর্বে আমেরিকা হতে বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা আমার নিকট এসেছিল। তাদের সাথে একজন বড়ুয়াও ছিল। তারা সেই বড়ুয়ার মাধ্যমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল-ভন্তে, মেয়েরা ভালো নাকি পুরুষেরা ভালো? তারা নাকি সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না। তাদেরকে আমি বলেছিলাম-যার চিত্তে বা যার নিকট জ্ঞান থাকে, সেই ভালো। পুরুষদের নিকট জ্ঞান থাকলে পুরুষেরা ভালো, আর মহিলাদের নিকট জ্ঞান থাকলে মহিলারা ভালো। অন্যদিকে যার নিকট জ্ঞান নেই সেই খারাপ। পুরুষদের নিকট জ্ঞান না থাকলে পুরুষেরা খারাপ এবং মহিলাদের নিকট জ্ঞান না থাকলে মহিলারা খারাপ। মোটকথা, যার নিকট জ্ঞান থাকে সেই ভালো, আর যার নিকট জ্ঞান নেই সেই খারাপ। যেই পুরুষের নিকট জ্ঞান থাকবে সেই পুরুষ ভালো এবং যেই মহিলার নিকট জ্ঞান থাকবে সেই মহিলা ভালো। অপরদিকে যেই পুরুষের নিকট জ্ঞান থাকবে না সেই পুরুষ খারাপ এবং যেই মহিলার নিকট জ্ঞান থাকবে না সেই মহিলা খারাপ। কেবল পুরুষেরা ভালো, মহিলারা খারাপ অথবা কেবল মহিলারা ভালো, পুরুষেরা খারাপ-এটা বলা যায় না। ভালো নাকি খারাপ-সেটা প্রমাণ হবে জ্ঞানের মাধ্যমে; পুরুষ-মহিলার বাহ্যিক পরিচয়ে নয়। তারা আমার উত্তর শুনে অত্যন্ত খুশি হয়। পরিতৃপ্ত মনে সেটা অনুমোদন করে চলে যায়। সবাই আমার সাথে বলো “চিত্তের মধ্যে জ্ঞান থাকলে পুরুষেরাও ভালো, মহিলারাও ভালো। আর চিত্তের মধ্যে জ্ঞান না থাকলে পুরুষেরাও খারাপ, মহিলারাও খারাপ।” মনে রাখবে, চিত্তের মধ্যে জ্ঞান থাকলে ভালো আর জ্ঞান না থাকলে খারাপ।
বনভন্তে আরো বলেন-জ্ঞান না থাকলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা যাবে না। তোমরা যদি অজ্ঞানী হও তাহলে স্বামী-স্ত্রী হয়ে সর্বদা পাপকর্ম সম্পাদন করেই চলবে। পুরুষেরা নারী চিত্ত হয়ে পড়বে আর নারীরা পুরুষ চিত্ত হয়ে পড়বে। পুরুষেরা নারীর পিছনে ঘুরবে আর নারীরা পুরুষের পিছনে ঘুরবে। পুরুষেরা নারী ছাড়া থাকতে পারবে না, নারীরা পুরুষ ছাড়া থাকতে পারবে না। পুরুষেরা নারীর প্রতি মোহিত হয়ে থাকবে, নারীরা পুরুষের প্রতি মোহিত হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমাদের নিকট যদি ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু উদয় হয় তাহলে তোমরা সেসব হতে নিজকে বিরত রাখবে। আর তখনই বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে সক্ষম হবে। এমন কি লোকোত্তর সুখ নির্বাণও আয়ত্ত করতে পারবে। লোকোত্তর সুখ লাভ করার প্রধান অন্তরায় হল স্বামী-স্ত্রী হয়ে কাম্য সুখ ভোগ করা। স্বামী-স্ত্রী হয়ে কাম্য সুখ ভোগে রত থাকলে লোকোত্তর সুখ নির্বাণ লাভ হয় না। আমার নিকট হতে এবম্বিধ উপদেশ শ্রবণ করে রাজ চন্দ্র বলেছিল-‘বেগ মিলেগুন মরি ন গেলে নির্বাণযে ন পারিবো। অর্থাৎ সব মেয়েরা মরে না গেলে নির্বাণ লাভ করা যাবে না। তার সে কথা শুনে মেয়েরা রেগে গিয়েছিল। তারা বলে উঠলো-‘সে নির্বাণ যাবে যাক, তজ্জন্য আমাদেরকে মরতে হবে কেন?আমরা মেয়েরা তাকে কি করলাম?’ রাজ চন্দ্রের কথা অনুসারে সব মেয়েরা মরে গেলে, কোন মেয়ে না থাকলে সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। কিন্তু সেটা তার অজ্ঞানের কথা। কারণ তার চিত্তে যদি অজ্ঞানতা থাকে তাহলে মেয়েরা সবাই মরে গেলেও সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। আর যদি তার চিত্তে জ্ঞান থাকে, মেয়েরা জীবিত থাকলেও সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ লাভ করার জন্য মেয়ে (বা পুরুষ) জীবিত থাকা-না থাকা কোন ব্যাপার নয়। চিত্তে জ্ঞান বিদ্যমান থাকাই আসল কথা। বনভন্তে সমবেত দায়ক দায়িকাগণকে প্রশ্ন করেন-মেয়েরা সবাই মরে গেলে কি রাজ চন্দ্র নির্বাণ লাভ করতে পারবে? দায়ক-দায়িকাবৃন্দ একবাক্যে বলে উঠে-”না ভন্তে, পারবে না। “বনভন্তে বলেন-রাজ চন্দ্রের কথা হল মেয়েরা সবাই মরে গেলে সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। এটা তার অজ্ঞানেরই কথা। কারণ চিত্তের মধ্যে যদি জ্ঞান থাকে তাহলে মেয়ে থাকলেও নির্বাণ লাভ করা যায়। অন্যদিকে চিত্তের মধ্যে যদি জ্ঞান না থাকে তাহলে সংসারে কোন মেয়ে না থাকলেও নির্বাণ লাভ করা যাবে না। মোটকথা হল, চিত্তের মধ্যে জ্ঞান থাকলে নির্বাণ লাভ করা যায়, আর চিত্তের মধ্যে জ্ঞান না থাকলে নির্বাণ লাভ করা যায় না। তজ্জন্য প্রথমেই বলেছি, বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে হলে জ্ঞানের প্রয়োজন। জ্ঞান না থাকলে বৌদ্ধধর্ম আচরণ করা যায় না। সেই জ্ঞান কি? কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত বি. এ., এম. এ., ডক্টরেট ডিগ্রী নয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিতে যে সকল বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয় তা তো সম্পূর্ণ পরের ধ্যান-ধারণা, সাধারণ জ্ঞান মাত্র। সেই পরের ধারণা দিয়ে প্রকৃত জ্ঞান, অসাধারণ জ্ঞানের উন্মেষ সম্ভব নয়। অসাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানীকে নিজের ভেতর থেকেই জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে হয়। আমি একটি ব্রহ্মদেশীয় পুস্তকেও (বঙ্গানুবাদ) পড়েছি-পরের মুখের কথায়, উপদেশ শ্রবণে, পুঁথিগত বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞান অর্জিত হয় না। নিজের বিবেক-বুদ্ধি-চিন্তা, বিচার-বিবেচনা, গবেষণার আলোকে অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। হ্যাঁ, সেই কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক। কারণ অগ্নিকণা বিহীন ছাঁইস্তুপে সারাদিন ফুঁ দিলেও কিছুতেই আগুন জ্বলে উঠবে না। জ্বলে উঠবে কি? “না ভন্তে, জ্বলে উঠবে না।” যেহেতু ছাঁইস্তুপে কোন অগ্নিকণা নেই। অন্যদিকে অগ্নিকণা বিশিষ্ট ছাঁইস্তুপে ফুঁ দিলে সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জ্বলে উঠবে। ঠিক তদ্রুপ তোমাদের চিত্তে যদি জ্ঞান না থাকে,আমি সারাদিন ধর্মদেশনা প্রদান করলেও তোমাদের কিছুই হবে না। আর তোমাদের চিত্তে যদি জ্ঞান থাকে, আমি ধর্মদেশনা প্রদান করলে তোমাদের সেই জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় উপাসক-উপাসিকাগণ এভাবেই বুদ্ধের নিকট ধর্মদেশনা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হতো। ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা প্রদান করার পূর্বে শ্রোতাগণের নিকট অন্তর্দৃষ্টিভাব উদয় হয়েছে কিনা তা দেখতেন। যখন দেখতেন শ্রোতাগণের নিকট অন্তর্দৃষ্টিভাব উদয় হয়েছে তখন তিনি স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু ইত্যাদি পারমার্থিক দেশনা প্রদান করতেন। আর শ্রোতাবৃন্দ স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ মার্গফলে অধিষ্ঠিত হতো। অন্তর্দৃষ্টিভাব উদয় না হলে ধর্মদেশনা প্রদান করলেও ধর্মদেশনার মর্মার্থ বুঝা যায় না। ধর্মদেশনা শ্রবণ করে মার্গফলাদি লাভ করা যায় না। ভগবান বুদ্ধ আন্দাজ (অনুমান) করে ধর্মদেশনা প্রদান করতেন না। শ্রোতাবৃন্দের চিত্তে অন্তর্দৃষ্টিভাব উদয় হলে তবেই তিনি ধর্মদেশনা প্রদান করতেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাবৃন্দের ধর্মচক্ষু, ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হতো। ধর্মজ্ঞান শব্দের অর্থ কুশলাকুশল ও লৌকিক-লোকোত্তর ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান। ধর্মজ্ঞান লাভ অর্থ স্রোতাপত্তি মার্গফলাদি লাভ করা। যাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হয় তাদের চারি অপায় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। যাদের ধর্মজ্ঞান, ধর্মচক্ষু লাভ হয় না, তাদের সর্বদা চারি অপায়ে পতনের সম্ভাবনা থেকেই যায়।
শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন-এক সময় শ্রীলংকা হতে আগত জনৈক ভিক্ষু আমাকে বলেছিল, ভন্তে আপনাকে সবাই বলে অর্হৎ। আচ্ছা, আসলেই কি আপনি অর্হৎ? আমি সেই ভিক্ষুকে বলেছিলাম-ভগবান বুদ্ধ উরুবেলা কাশ্যপকে ১০৮টি ঋদ্ধি প্রদর্শন করেছিলেন। তারপরও উরুবেলা কাশ্যপ ভেবেছিল-শ্রমণ গৌতমের ঋদ্ধি রয়েছে, সে মহাঋদ্ধিশালী বটে। কিন্তু এখনও অর্হৎ হতে পারেন নাই। তখন ভগবান বুদ্ধ উরুবেলা কাশ্যপকে বলেছিলেন-মূর্খ, তুমি চিরকালই ভাববে গৌতম অর্হৎ নন। সঙ্গে সঙ্গে উরুবেলা কাশ্যপ ভগবানের পদে শির ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। আর বুদ্ধের নিকট শিষ্যত্ব্ গ্রহণ করেন এবং তৃষ্ণাক্ষয় সাধন করে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। কাজেই বাইরের শরীর দেখে তুমি কেমনে অর্হৎ চেনবে? তখন সেই ভিক্ষু বলেছিল-হ্যাঁ ভন্তে,আপনার কথা সঠিক। সে আরো বলেছিল-অর্হৎগণের উপাদান থাকে না, স্কন্ধ থাকে। সে আরো কি বলেছিল? ‘অর্হৎগণের উপাদান থাকে না,পঞ্চস্কন্ধ থাকে।’ অর্হৎগণের পঞ্চস্কন্ধ কিভাবে থাকে জান? অনাসক্তভাবেই থাকে। অর্হৎগণ পঞ্চস্কন্ধে অনাসক্তভাবেই থাকেন বা অনাসক্তভাবে পঞ্চস্কন্ধে অবস্থান করেন। পঞ্চস্কন্ধে অবস্থান না করলে অরহতকেও মরে যেতে হবে। কারণ পঞ্চস্কন্ধকে আশ্রয় করেই তো জীবনের অস্তিত্ব। তবে অরহতেরা পঞ্চস্কন্ধে সুখ ভোগ করে না। যেমন-তোমরা দান দিতেছ, আমি দান গ্রহণ করছি। কোথায় গ্রহণ করছি? পঞ্চস্কন্ধে করছি। পঞ্চস্কন্ধে দান গ্রহণ না করলে তো দান গ্রহণ করাই সম্ভব হবে না। অর্হৎগণ পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত থাকেন না, তাই তারা সুখেই থাকেন। কিন্তু যারা অর্হৎ নয় তারা পঞ্চস্কন্ধের প্রতি আসক্ত হয়েই থাকে (বা অবস্থান করে)। তাই তারা দুঃখ পায়। তোমরাও অর্হৎ নয় বলে পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত হয়ে অবস্থান করছ। পঞ্চস্কন্ধকে নিয়ে সুখ ভোগ করছ। ফলে বর্ণনাতীত দুঃখ ভোগ করেই চলেছ। মনে রাখবে,অর্হৎগণ পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত থাকেন না। যারা অর্হৎ নয় তারা পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত থাকে। অর্হৎগণ পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত নয় বলে তারা পুনর্জন্ম ধারণ করেন না। কিন্তু যারা অর্হৎ নয় তারা পঞ্চস্কন্ধে আসক্ত বলে পুনর্জন্ম ধারণ করে।
প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম আচরণ করতে চাইলে স্বামী-স্ত্রী হয়ে সাংসারিক জীবন যাপন করা যায় না। কোন মহিলা কোন পুরুষের স্ত্রী হতে পারবে না। কোন পুরুষ কোন মহিলার স্বামী হতে পারবে না। কারোর স্ত্রী হলেই দুঃখ পেতে হয়, পাপ অর্জিত হয়। কারোর স্বামী হলেই দুঃখ পেতে হয়, পাপ অর্জিত হয়। কারোর স্ত্রী না হলেই সুখ, পুণ্য; কারোর স্বামী না হলে সুখ, পুণ্য হয়। এটাই হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ত্যাগ করে সাংসারিক জীবন যাপন না কর; কোন পুরুষ কোন মহিলার স্বামী না হও এবং কোন মহিলা কোন পুরুষের স্ত্রী না হও, এককথায় লৌকিক সুখ ভোগ পরিত্যাগ কর তাহলে নির্বাণ লাভ করতে পারবে। পরিশেষে তিনি বলেন-তোমরা সর্বদা জ্ঞানের সহিত অবস্থান কর। জ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে কখনো পরিহানি হয় না। অধোপতনে পতিত হতে হয় না, দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয় না। প্রতি পলে পলে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ অর্জিত হতে থাকে। তোমরা কখনো অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করবে না। অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করলে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে না। সুখ লাভ হবে না। সুখ লাভ করা সুদূর পরাহত হবে। অজ্ঞানের সহিত অবস্থান করাটা কি রকম জান? পরিহানি হবার কাণ্ড, অধোপতনে পতিত হবার কাণ্ড, দুঃখ পাবার কাণ্ড, ঠকে যাওয়ার কাণ্ড, পরাজিত হবার কাণ্ড। আর জ্ঞানের সহিত অবস্থান করাটা কি রকম? উন্নতি করার কাণ্ড, শ্রীবৃদ্ধি লাভের কাণ্ড, সুখ পাবার কাণ্ড, উতরে যাওয়ার কাণ্ড, জয়ী হবার কাণ্ড। তোমরা সবাই বলো “আমরা জ্ঞানের সহিত অবস্থান করব, অজ্ঞানতার সহিত অবস্থান করব না”। তাহলে তোমাদের সুখ লাভ হবে, উন্নতি-শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হবে। তোমরা সর্বদিকে জয়যুক্ত হতে পারবে।
সাধু, সাধু, সাধু।
লেখকঃ ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত মহাস্থবির, অধ্যক্ষ, রাজবন ভাবনা কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি। আর্যশ্রাবক বনভন্তের ধর্মদেশনা সিরিজ গ্রন্থপ্রণেতা সহ অনেক বাংলা ত্রিপিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদক।
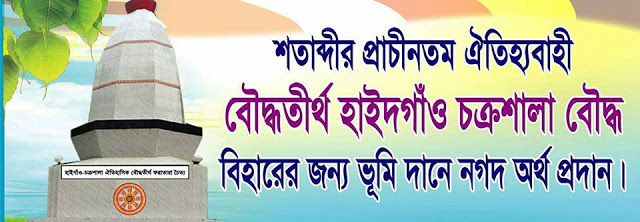
by admin | Jan 7, 2019 | blog
যুগে যুগে বঙ্গ বা বাঙালি শব্দকে ঘিরে সুজলা-সুফলা অস্তিত্বকে কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকরা ভাবের ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত করে আসছেন। ইবনে বতুতা, আলবেরুণী, টলেমী ও চৈনিক পর্যটকগণ বাংলার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। কিন্তু সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক সময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন “বাঙালির ইতিহাস নাই”। সত্যিকার অর্থেই আমরা বাঙালিরা ইতিহাস জিজ্ঞাসু নই। আর তাই কালের করাল গ্রাসে এই নশ্বর পৃথিবীর সবকিছুই অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যায়। আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে আমাদের চারপাশের পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইতিহাস সংগ্রহ করে আমরা নিজেদের সভ্যতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারি যা যুগে যুগে প্রেরণার উপকরণ হিসেবে সৃজনশীল কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। আমরা একটু দৃষ্টি দিই আদি বৌদ্ধতীর্থ চক্রশালার দিকে।
দক্ষিণ চট্টগ্রামের অগ্রসরমান জনপদ পটিয়া। পটিয়া সদর থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার পূর্বে এর অবস্থান। বৌদ্ধযুগে চট্টগ্রামের আদি নাম ছিল চট্টলা। তবে এটি চক্রশালা নামেই বহির্জগতে সমধিক পরিচিত ছিল এবং এখনো বিদ্যমান। বর্তমানে এই চক্রশালা গ্রামটি এর ক্ষীণ স্মৃতি বহন করে বৈকি। পূর্বে এ স্থানে শুধু একটি মন্দির ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই মন্দিরের গায়ে মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা আছে, “ফরাতারা স্তুপ নবতর পর্যায়ে সংস্কার ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ চক্রশালা বৌদ্ধতীর্থ সংরক্ষণ কমিটি হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।” পর্যায়ক্রমে এ স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে একটি সুদৃশ্য তোরণ ও সীমানা প্রাচীর। এছাড়া এ মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছে একটি পাকাঘাটসমেত পুকুর ও টিউবওয়েল। বলাবাহুল্য এ মন্দিরের আশেপাশে এমনকি হাইদগাঁও ও চক্রশালা গ্রামের কোথাও বৌদ্ধ পরিবারের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু জনশ্র“তি আছে এখানে একসময় বৌদ্ধদের বাস ছিল যা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়।
এই চক্রশালা নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা মহলের কাছ থেকে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। শোনা যায় এ স্থানে তথাগত গৌতম বুদ্ধ সুদূর রেঙ্গুন (মিয়ানমার) থেকে আসার পথে অবকাশ যাপন করেন এবং তিনি চংক্রমন করেছিলেন বলেই এই স্থানটিকে চক্রশালা নামে অভিহিত করা হয়। কেউ কেউ বলেন চক্রশালায় বুদ্ধের বত্রিশ লক্ষণ ও অশীতি অনুরঞ্জন অঙ্কিত বুদ্ধচক্র নামক পাথর, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য শীলভদ্র মহাস্থবিরের শিষ্য দীপঙ্কর স্থবির কর্তৃক এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেজন্য একে চক্রশালা বলা হয়। উল্লেখ্য, তিব্বতের তাঞ্জুর গ্রন্থেও চক্রশালার ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে জানা যায়। তবে ভদন্ত ধর্মতিলক ও বীরেন্দ্র মুৎসুদ্দী কর্তৃক অনুবাদিত সদ্ধর্ম রত্নাকর গ্রন্থে যা লিপিবদ্ধ আছে সে তথ্যগুলোকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলে বিবেচনা করা হয়। তা এই রকম চট্টল বৌদ্ধগণের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ না থাকলেও শ্র“তি পরম্পরা ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ প্রাচীনদের মতে চট্টল বৌদ্ধদের আদি পুরুষ মগধ হতে এসেছে। ছান্ধমা নামে এক ব্যক্তি মগধ দেশ হতে এসে প্রথমে আকিয়াবের ছান্ধমা পাহাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁর নামানুসারে সেই পাহাড়ের নাম ছান্ধমা নামে আজো পরিচিত। তিনি সেই পাহাড়ের শীর্ষে এক মনোরম ধাতুচৈত্য নির্মাণ করেন। প্রবাদ আছে সেই ধাতুচৈত্য হতে সময়ে সময়ে জ্যোতি নির্গত হয়। ঐ আদিপুরুষ ছান্ধমার চেন্দি ও রাজমঙ্গল নামে দুই পুত্র ছিল। চেন্দি ছিলেন গৃহী আর রাজমঙ্গল ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গৃহী চেন্দীর ঔরসে কেজগ্রি, কেয়ক্চু ও বৃন্দাবন নামে তিনটি সন্তানের জন্ম হয়। তাদের বাসস্থান ছিল কক্সবাজারের চকরিয়া গ্রামে। তাদের মধ্যে কেয়ক্চু মগধবাসী দীপঙ্কর মহাস্থবিরের শিষ্য সরভূ মহাস্থবিরের নিকট ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নামকরণ হয়েছিল চন্দ্রজ্যোতিঃ।
এরপর তিনি দেশপরিভ্রমণ ও শিক্ষালাভের মানসে ব্রহ্মদেশের মৌল মেইনে গমন করেন। সেখানে বিশ বছর যাবত ধর্ম, বিনয় অধ্যয়ন করে দেশে ফেরার সময় সেদেশের দশজন ভিক্ষুসহ একটি চক্রাসন, তিনটি বুদ্ধমূর্তি ও কয়েক খণ্ড বুদ্ধাস্থি এনেছিলেন। উল্লেখ্য, সেই বুদ্ধমূর্তিগুলো আনয়নের সুবিধার জন্য তিন টুকরা অবস্থায় আনা হয়েছিল বলে ত্রিভঙ্গ মূর্তি নামে কথিত রয়েছে। মূর্তিগুলোর শিরোপরি বুদ্ধের শারীরিক অস্থিধাতু স্থাপিত ছিল। তাঁরা আগরতলার লালমাই পাহাড়ে বিহার স্থাপন করেন। আগরতলা রাজবংশীয় বলিভীম আদিত্য নামক জনৈক শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি তাঁদের জন্য বিহার নির্মাণ করে সেখানে চৌদ্দ হাত লম্বা পরিনির্বাণ মূর্তি ও বিনয়ানুকুল ভিক্ষুসীমা নির্মাণ করেছিলেন। সেই সীমায় ক্রমে ১০০ জনকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে পাঁচ বৎসরকাল শিষ্যদেরকে ধর্মবিনয় শিক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে ফিরছিলেন, ফেরার পথে সীতাকুন্ড পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে একটি বিহার স্থাপন করেন। সেখানে পূর্বোক্ত ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি স্থাপনপূর্বক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে সীতাকুন্ড পাহাড় ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতিঃ বিহারের নামানুসারে চন্দ্রশেখর নামে পরিচিত হয়ে আসছে।
এরপর তিনি শিষ্যগণসহ পটিয়ার পর্বত নির্ঝরণী শ্রীমতির তীরে হাইডমজা নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির আম্রকাননে উপস্থিত হন। হাইডমজা খবর পেয়ে প্রতিবেশীসহ চন্দ্রজ্যোতি স্থবিরকে দেখতে যান। তিনি স্থবিরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলাপে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আপন বিহারে নিয়ে যান এবং তিন দিনব্যাপী ধর্মসভার আয়োজন করেন। হাইডমজা কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলেন যে, এই স্থবির কক্সবাজারের চকরিয়া নিবাসী চেন্দির পুত্র। অতঃপর তিনি এ সংবাদ নিয়ে চকরিয়াতে লোক পাঠালেন। চেন্দি নিরুদ্দেশ পুত্রের খবর পেয়ে খুবই পুলকিত হলেন এবং অনেক লোকজন সমভিব্যহারে গিয়ে পুত্রকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনেন।
চকরিয়াতে রওয়ানা হবার সময় হাইডমজা চন্দ্রজ্যোতি স্থবিরের নিকট চক্রাসনটি প্রার্থনা করেন। স্থবিরও তা তাকে সানন্দে প্রদান করেন। এই চক্রাসন স্থাপনের জন্য হাইডমজার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নিজ গ্রামের কেন্দ্রে যে মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তা-ই চক্রশালা মন্দির। চক্রাসন স্থাপনের জন্য এই এলাকাটি “চক্রশালা” নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এরপর স্থবির পুনরায় তার পিতাসহ এই এলাকায় চক্রাসনের মন্দির বন্দনার মানসে উপস্থিত হন। সেখানে বন্দনা, পূজা করে বিষুব সংক্রান্তিতে মেলার আয়োজন করেন। সেই থেকেই প্রতি বছর এই স্থানে চৈত্র মাসের শেষদিন অর্থাৎ বিষুব সংক্রান্তিতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।
কালের বিবর্তনে চক্রশালা আদি বৌদ্ধ তীর্থ মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে পরলোকগত সংঘরাজ পূর্ণাচার ধর্মাধার চন্দ্রমোহন মহাস্থবির ও প্রত্নতত্ত বিশারদ জগতচন্দ্র মহাস্থবিরের প্রয়াসে পুনঃনির্মিত হয়। দ্বিতীয়বারে পটিয়ার বাকখালী গ্রামের প্রয়াত নবীন চন্দ্র বড়ুয়ার উদ্যোগে সাধারণের অর্থানুকুল্যে মন্দিরটি সংস্কার করা হয় এবং সাতবাড়িয়ার প্রয়াত অধীন চন্দ্র চৌধুরী মন্দিরের সম্মুখস্থ পুকুরের পক্ষোদ্ধার করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পটিয়ার মধ্যম জোয়ারা গ্রামের প্রয়াত মনোরঞ্জন বড়ুয়া নিজ ব্যয়ে পুকুরের ঘাট নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপন করেন।বাংলাদেশী বৌদ্ধ কল্যাণ সমিতি কুয়েতের অর্থায়ণে মন্দিরের প্রবেশ পথে একটি সুউচ্চ ও নান্দনিক তোরণ নির্মাণ করা হয়।
বিষুব সংক্রান্তির মেলায় এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ জুড়ে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণের সমাগম ঘটে। আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব এরকম ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানের গুরুত্ব অক্ষুন্ন রাখতে উদ্যোগী হওয়া। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্পসমেত উদ্যোগ গ্রহণে সরকারী অনুদান ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসা একান্ত অপরিহার্য। না হয় প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন এই অতীত গৌরব বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে।
Copypost – attabinshotitimes.blogspot.com

by admin | Jan 1, 2019 | jatok
পুরাকালে বিদেহের অন্তঃপাতী মিথিলা নগরীতে মদেব নামক এক ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। প্রথমে কুমার, পরে উপরাজ, শেষে মহারাজভাবে তিনি একাদিক্রমে বিরাশি। হাজার বৎসর পরমসুখে অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি নাপিতকে বলিলেন, “আমার মাথায় যখন পাকা চুল দেখিতে পাইবে, তখন আমায় জানাইবে।” ইহার বহুবৎসর পরে একদিন নাপিত রাজার কজ্জল-কৃষ্ণ কেশরাশির মধ্যে একগাছি পলিত কেশ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জানাইল। রাজা বলিলেন, “চুলগাছি তুলিয়া . আমার হাতে দাও।” তখন নাপিত সােণার সয়া দিয়া ঐ চুলগাছি তুলিয়া রাজার হাতে দিল। মখাদেবের তখনও চুরাশি হাজার বৎসর পরমায়ুঃ অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু একগাছি মাত্র পাকা চল দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বৈকল্য জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, মৃত্যুরাজ যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, অথবা তিনি দহমান পর্ণশালার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘মূখ মখাদেব! পাপবৃত্তি পরিহার করিবার পূর্বেই পলিত-কেশ হইলে! তিনি পলিত কেশের সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তঁাহার অন্তর্দাহ হইতে লাগিল, শরীর হইতে ঘর্ম ছুটিল ; রাজবেশ ও রাজাভরণ দুর্বিষহ বােধ হইতে লাগিল। তিনি স্থির করিলেন, ‘অদ্যই সংসার ত্যাগ পূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব।” মহাদেব নাপিতকে, এক লক্ষ মুদ্রা আয় হয়, এমন একখানি গ্রাম দান করিলেন এবং নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “বৎস, আমার কেশ পলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি এতদিন পূর্ণমাত্রায় মনুষ্যকাম্য ভােগ করিয়াছি ; এখন দেবকাম্য ভােগ করিব। আমার নিমণ-কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি মখাদেম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া শ্ৰমণ-বৃত্তি অবলম্বন করিব।” রাজাকে প্রব্রজ্যাবলম্বনে কৃতদ্যোগ দেখিয়া অমাত্যগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আপনি সংসার ত্যাগ করিতেছেন কেন?” রাজা সেই পলিত কেশটী হাতে লইয়া বলিলেন,
“দেবদুত আসিয়াছে করিতে আয়ুর শেষ,
মস্তক উপরি ধরি পলিত কেশের বেশ।
আর কেন থাকি মিছা বদ্ধ হয়ে মায়াপাশে ? .
প্রব্রজ্যা লইব আজি মুকতি-লাভের আশে।”
অনন্তর সেই দিনই তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রব্রাজক হইলেন এবং উক্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেখানে চুরাশি হাজার বৎসর তপস্যা করিতে করিতে মখাদেব পূর্ণজ্ঞানে ব্ৰহ্মলােক প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ব্রহ্মলােক ত্যাগ করিয়া মিথিলার রাজরূপে জন্মগ্রহণ-পূৰ্ব্বক তিনি “নিমি” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আত্মকুলের সকলকে একত্র করিয়া এ জন্মেও তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন এবং সেই আম্রকাননে বাস করিয়া ব্ৰহ্মবিহার * ধ্যান করিতে করিতে পুনৰ্ব্বার ব্রহ্মলােকে চলিয়া যান।
সুত্র ঃ জাতকসমগ্র

by admin | Jan 1, 2019 | jatok
পুরাকালে বারাণসী-রাজ ব্ৰহ্মদত্ত একদিন উদ্যানবিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ফলপুস্পাদির আহরণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন দেখিতে পাইলেন, একটী রমণী গান করিতে করিতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিতেছে। ব্ৰহ্মদত্ত তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই তাহাকে গান্ধৰ্ববিধানে বিবাহ করিলেন। অনন্তর বােধিসত্ত্ব এই রমণীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ‘রমণীকে গর্ভবতী জানিয়া রাজা তাহার হস্তে স্বনামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরী দিয়া বলিলেন, “যদি কন্যা প্রসব কর, তবে ইহা বিক্রয় করিয়া তাহার ভরণ পোেষণ করিবে ; আর যদি পুত্র প্রসব কর, তবে তাহাকে এই অঙ্গুরিসহ আমার নিকট লইয়া যাইবে।রমণী যথাকালে বােধিসত্ত্বকে প্রসব করিল। বােধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিয়া পাড়ার ছেলেদের সহিত খেলা আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে তাঁহাকে “নিষ্পিতৃক” বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কেহ বলিত “দেখ, নিম্পিতৃক আমাকে মারিয়া গেল,” কেহ বলিত, “নিষ্পিতৃক আমাকে ধাক্কা দিল।” ইহাতে বােধিসত্বের মনে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি একদিন জননীকে জিজ্ঞাসিলেন, “আমার বাবা কে, মা ? রমণী বলিল, “বাছা, তুমি রাজার ছেলে।” “আমি যে রাজার ছেলে তাহার প্রমাণ কি, মা ?” “বাছা, রাজা যখন আমায় ছাড়িয়া যান, তখন এই অঙ্গুরি দিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার নাম আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, যদি কন্যা জন্মে, তবে ইহা বেচিয়া তাহার ভরণ পােষণ করিবে, আর যদি পুত্র জন্মে, তবে অঙ্গুরিসহ তাহাকে আমার নিকট লইয়া যাইবে।”“তবে তুমি আমাকে বাবার কাছে লইয়া যাওনা কেন?” রমণী দেখিল, বালক পিতৃদর্শনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। সুতরাং সে তাহাকে লইয়া রাজভবনে উপনীত হইল এবং রাজাকে আপনাদের আগমনবার্তা জানাইল। অনন্তর রাজসকাশে যাইবার অনুমতি পাইয়া সে সিংহাসনপার্শ্বে গিয়া প্রণিপাতপূৰ্ব্বক বলিল, “মহারাজ, এই আপনার পুত্র।” সভার মধ্যে লজ্জা পাইতে হয় দেখিয়া, রাজা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিয়াও না জানার ভাণ করিলেন। তিনি বলিলেন “সে কি কথা? এ আমার পুত্র হইবে কেন?” রমণী কহিল, “মহারাজ, এই দেখুন আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরি। ইহা দেখিলেই বালক কে জানিতে পারিবেন।” রাজা এবারও বিস্ময়ের চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন, “এ অঞ্চুরি ত আমার নয়।” তখন রমণী নিরুপায় হইয়া বলিল, “এখন দেখিতেছি, একমাত্র ধর্ম ভিন্ন আমার আর কোন সাক্ষী নাই। অতএব আমি ধর্মের দোহাই দিয়া বলিতেছি, যদি এ বালক প্রকৃতই আপনার পুত্র হয়, তবে যেন এ মধ্যাকাশে স্থির হইয়া থাকে, আর যদি আপনার পুত্র না হয়, তবে যেন ভূতলে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।” ইহা বলিয়া সে দুই হাতে বােধিসত্ত্বের দুই পা ধরিল এবং তাঁহাকে ঊর্ধদিকে ছুড়িয়া দিল। | বােধিসত্ত্ব মধ্যাকাশে উঠিয়া বীরাসনে উপবেশন করিলেন এবং মধুর স্বরে ধর্মকথা বলিতে বলিতে এই গাথা পাঠ করিলেন; আমি তব পুত, শুন মহারাজ, ধর্মপত্নীগর্ভজাত ; পােষণের ভার লও হে আমার, এ মিনতি করি, তাত। কত শত জন ভরণ-পােষণ লভে নৃপতির ঠাই ; তাঁহার তনয় যেই জন হয়, তার ত কথাই নাই। আকাশ বােধিসত্বের মুখে এই ধর্ম-সঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাজা বাহুবিস্তার পূর্বক বলিলেন, “এস, বৎস, এস ; এখন অবধি আমিই তােমার ভরণ পােষণ করিব।” তাহার দেখাদেখি আরও শত শত লােকে বােধিসত্বকে ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহু তুলিল, কিন্তু বােধিসত্ত্ব রাজারই বাহুযুগলের উপর অবতরণ করিয়া তাহার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। রাজা তাহাকে ঔপরাজ্যে নিযুক্ত করিলেন এবং তাহার জননীকে মহিষী করিলেন। কালক্রমে রাজার যখন মৃত্যু হইল, তখন বােধিসত্ত্ব “মহারাজ কাষ্ঠবাহন” এই উপাধি গ্রহণপূর্বক সিংহাসনারােহণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল যথাধর্ম রাজ্যশাসন করিয়া কৰ্ম্মানুরূপ ফলভােগাৰ্থ লােকান্তরে চলিয়া গেলেন।
সুত্র ঃ জাতকসমগ্র